নদী ও পরিবেশ রক্ষায় রাজনৈতিক অঙ্গিকার জরুরি

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে আজ অবধি যেসব বিষয় সবচেয়ে বেশি হুমকির মধ্যে পতিত হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো নদী ও পরিবেশ, যা রক্ষায় রাজনৈতিক অঙ্গিকার জরুরি।
এভাবে চলতে চলতে পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত হওয়ার বিপরীতে দেশে নেমে এসেছে ভয়াবহ বিপর্যয়। নদীর ক্ষেত্রেও ভিন্নতর কিছু নয়। কিন্তু কেন এমন পরিস্থিতি তৈরি হলো? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে জানা যায়, এর পেছনে প্রধানতম দায় হলো রাজনৈতিক নেতৃত্বের।
কেন? সে কথা বোধ করি ব্যাখ্যা করে বলার খুব বেশি প্রয়োজন নেই। বিগত সাড়ে পাঁচ দশকে সরকারের পক্ষে নদী ও পরিবেশের সুরক্ষায় যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দায়িত্বশীল ছিলেন, তারা কে কতটুকু দায়িত্ব পালন করেছেন, তা কম-বেশি আমরা সবাই জানি।
নদী ও পরিবেশের বর্তমান অবস্থা
গত ২৬ অক্টোবর পত্রিকার খবর হলো—ঢাকার ৮টি স্থানে বায়ুর মান আজ বেশ খারাপ। এদিন সকালে বায়ুদূষণে বিশ্বের ১২৭টি নগরীর মধ্যে ঢাকার অবস্থান চতুর্থ। সকালের দিকে আইকিউএয়ার-এর তথ্য অনুযায়ী ঢাকার গড় বায়ুমান দাঁড়ায় ১৬৩। যাকে খুবই অস্বাস্থ্যকর হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
এটিই প্রথম নয়, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বায়ুদূষণে আমাদের অবস্থান প্রথম দিকেই থাকছে। এই বায়ু দূষণের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত দেশের মাটি, পানি দূষণ হচ্ছে, হচ্ছে ভয়ংকর শব্দ দূষণও।
ক্রমাগত কাটা হচ্ছে পাহাড়, উজাড় হচ্ছে বন। এসব স্থানে গড়ে তোলা হচ্ছে বসত বাড়ি, শিল্প কারখানা ও ইটের ভাটা, পিকনিক স্পট, শুটিং স্পট, বাগান বাড়ি, খামার বাড়ি। এই পাহাড় আর বন ধ্বংস করার কারণে বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক জীবনযাপন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। প্রায়ই খবরের কাগজে সংবাদ প্রকাশ হয় 'বনের প্রাণী লোকালয়ে কেন?'
অন্যদিকে বাংলাদেশের ফুসফুস খ্যাত সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য আজ ধ্বংসের মুখে। প্রতিনিয়ত নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করার পরেও তার কোনো মূল্য আমাদের কাছে নেই। নির্বিচারে কাটা হচ্ছে গাছ, অবৈধ জাল ও বিষ দিয়ে করা হচ্ছে মাছ শিকার, হরিণসহ নানা বন্যপ্রাণী শিকার, সেইসঙ্গে বনের ভেতরে আগুন দেওয়াসহ নানা অপকর্মে ক্রমে ক্রমে বনটিকে নিঃশেষ করা হচ্ছে।
গত ২৭ আগস্ট দৈনিক খবরের কাগজ পত্রিকা 'মিলেমিশে পাহাড় সাবাড়' শিরোনামে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনের প্রথম অংশে বলা হয়েছে, 'ব্যাপকহারে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পর চট্টগ্রামে যে কয়টি পাহাড় এখনো টিকে আছে সেগুলো অতি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। কোনোটার চারপাশ ৯০ ডিগ্রি খাড়াভাবে কাটা হয়েছে। কোনোটার ওপর থেকে কাটা হয়েছে। এভাবে পাহাড় কাটায় ধীরে ধীরে নষ্ট হচ্ছে চট্টগ্রামের পরিবেশের ভারসাম্য। ভেঙে পড়ছে বাস্তুসংস্থান।'
'তবে এই কাজটি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একা করছে না। সম্মিলিতভাবে কাটা হচ্ছে পাহাড়। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ভূমিদস্যু, মাটিখেকো, শিল্পগ্রুপ এবং রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাহাড় কাটায় ভূমিকা রেখেছেন। এ ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন, জেলা প্রশাসনসহ সরকারি সংস্থাগুলো নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। এসব সংস্থা কোথাও কোথাও নিজেরাই পাহাড় কেটেছে। অর্থাৎ রক্ষক হয়েছে ভক্ষক।'
বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের আয়োজনে গত ২ নভেম্বর “নদী ও পরিবেশ রক্ষায় রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে প্রত্যাশা” শীর্ষক এক আলোচনাসভা হয়। ছবি, ফেসবুক থেকে
শুধু চট্টগ্রাম নয়, খোদ ঢাকার বুকে সবুজে বেষ্টিত খেলার মাঠ ও পার্কগুলোতে নানা রকমের প্রায় অপ্রয়োজনীয় স্থাপনা প্রতিষ্ঠার নামে দখল করে ধ্বংস করা হচ্ছে পরিবেশ। শহরের বুক জুড়ে সবশেষ যে ৫৮টি পুকুর ছিল, তারও প্রায় ৩১টি ভরাট হয়ে গেছে।
এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঢাকার চারপাশের চার নদীর—বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা—তীব্র দূষণ। যে কারণে বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে দেশের রাজধানী শহর।
ঢাকার ফুসফুস খ্যাত 'ওসমানী উদ্যান' ও রাজধানীর সার্ক ফোয়ারা মোড়সংলগ্ন 'পান্থকুঞ্জ পার্ক' নিঃশেষের দারপ্রান্তে। পরিবেশবাদীদের তীব্র বাধা উপেক্ষা করে সরকার পার্ক দুটোতে স্থাপনা নির্মাণ করে যাচ্ছে।
গত সেপ্টেম্বরে 'পান্থকুঞ্জ পার্ক' ও হাতিরঝিল জলাধারের উন্মুক্ত স্থানে যেকোনো ধরনের নির্মাণকাজ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে পান্থকুঞ্জ পার্ক ও হাতিরঝিলে বিনোদন ও অন্য উদ্দেশ্যে জনসাধারণের প্রবেশাধিকারে হস্তক্ষেপ না করতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
কিন্তু এরপরও পান্থকুঞ্জ পার্কে স্থাপনা নির্মাণের তৎপরতা চলমান। আমরা যাবো কোথায়? প্রায় চার কোটি মানুষের বসবাসের এই নগরীকে কংক্রিটের জঞ্জালে পরিণত করার অপচেষ্টা কোনোভাবেই রোখা সম্ভব হচ্ছে না।
আমরা নদী দখল-দূষণেও পিছিয়ে নেই, ক্রমশ অগ্রসরমান। নদীমাতৃক এই দেশে নদীই এখন সবচেয়ে বেশি অবহেলার শিকার। অথচ ২০১৯ সালে তুরাগ নদ সংক্রান্ত এক মামলায় হাইকোর্ট নদীকে 'জীবন্ত সত্ত্বা' হিসেবে রায় দিয়েছেন। আদালত বলেছেন, নদীর বাঁচা-মরার ওপর বাংলাদেশের অস্তিত্ব জড়িত। বাঁচলে নদী বাঁচবে দেশ, বাঁচবে প্রিয় বাংলাদেশ।
নদীর আইনি সত্ত্বা তৈরি হওয়ার পরও দখল-দূষণ আর দায়িত্বহীনতার কারণে ইতোমধ্যে হারিয়ে গেছে অনেক নদী। সংখ্যার হিসেবে তা ঠিক কত, আমাদের জানা নেই।
গণমাধ্যম সূত্রে প্রায় প্রতিদিনই দেশের কোথাও না কোথাও নদী দখল, বালু উত্তোলন কিংবা দূষণের সংবাদ পাওয়া যায়। এই দখলের তালিকায় স্থানীয় প্রভাবশালী, রাজনৈতিক নেতা কিংবা বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান—কেউ বাদ যায়নি। কোথাও কোথাও নদীকে খাল দেখিয়ে প্রকল্প তৈরি করে সেই খাল খননের নামে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রভাবশালী ব্যক্তি।
দূষণের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই ভরাট হচ্ছে নদী। ধীরে ধীরে মানচিত্র থেকে মুছে যাচ্ছে শেষ চিহ্নটুকুও। এসব কারণে আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতি সামাল দেওয়াও আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশেষত ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা অঞ্চলে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পেছনে অন্য অনেক কারণের সঙ্গে নদীর নাব্যতা সংকট গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।
নদ-নদী দেশের কাছে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিদের দরদ দেখেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দেশে কমছে নদ-নদীর সংখ্যা। বিদ্যমান পরিস্থিতি নদীর সঠিক সংখ্যা কত, তারও কোনো নিশ্চিত উত্তর আমাদের কাছে এই মুহূর্তে নেই।
তবে চলতি বছরের এপ্রিলের মাঝামাঝি বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, দেশের নদ-নদীর সংখ্যা ১ হাজার ৪১৫টি। আমরা জানতে পারি, সরকারের দুটি মন্ত্রণালয় ও তিনটি সংস্থা এবং নদীকর্মীদের সমন্বয়ে এটি প্রস্তুত করা হয়েছে।
তারপরেও তালিকাটি সব মহলে গ্রহণযোগ্য হয়নি। এই তালিকা নিয়েও একাধিক নদী বিশেষজ্ঞ আপত্তি জানিয়েছেন।
শুধু কি দেশের মোট নদীর তালিকা নিয়েই প্রশ্ন? না। এই প্রশ্ন দেশের আন্তঃসীমান্ত নদীর তালিকা নিয়েও রয়েছে। যৌথ নদী কমিশনের হিসাবে, বাংলাদেশে প্রায় ৫৭টি আন্তঃসীমান্ত নদী রয়েছে। এরমধ্যে বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তে ৫৪টি এবং বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সীমান্তে ৩টি। এই সংখ্যার প্রতি ভিন্নমত পোষণ করে দেশের নদীকর্মীরা বহুদিন ধরে নতুন করে জরিপের মাধ্যমে সঠিক তালিকা প্রণয়নের দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু সেই দাবি আজও অপূর্ণই থেকে গেল।
নদী জরিপ, তালিকা প্রণয়ন—এসবের বাইরে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পানির 'ন্যায্য হিস্যা'। বাংলাদেশ ভাটির দেশ হয়েও উজানের দেশ ভারতের কাছ থেকে নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে পারছে না বা ব্যর্থ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিস্তা আমাদের সামনে একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। এর মধ্যে আগামী বছরই সামনে আসছে গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি প্রসঙ্গ। ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে 'গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি'র মেয়াদ শেষ হতে যাচ্ছে।
নদী, পরিবেশের এই বেহাল দশার সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব তো আছেই। বাড়ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা, বজ্রপাত, উষ্ণায়ন, অতিবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ। কমছে খাদ্য উৎপাদন, বাড়ছে অসুখ-বিসুখ। একই সঙ্গে গৃহহারা হচ্ছে অগণিত মানুষ—যা আমাদের জন্য চরম অশনি সংকেত।
এই যে পানির দেশে, নদীর দেশে নদীর প্রতি অবহেলা, তা কোনোভাবে আমাদের প্রাণ-প্রকৃতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। উচিৎ হচ্ছে দেশের নদ-নদী সুরক্ষায় রাষ্ট্রের অতীব যত্নবান হওয়া। আর সেটা নিশ্চিত করার পেছনে মূল ভূমিকা রাখতে পারে রাজনৈতিক সদিচ্ছা।
দেশের নদ-নদী, হাওর, জলাধার, পাহাড়, বনাঞ্চল সুরক্ষায় ও জলবায়ুর অভিঘাত থেকে বাঁচতে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা দলের গঠনতন্ত্র ও আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে প্রণীত ইশতেহারে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে।
সত্যি বলতে, রাজনৈতিক দলগুলো আন্তরিকভাবে না চাইলে নদী ও পরিবেশের সুরক্ষা সম্ভব নয়। তাই আমরা চাই, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের এজেন্ডার অগ্রভাগে রাখুক নদী ও পরিবেশের সুরক্ষা প্রসঙ্গ।
প্রস্তাবনা
নদী-পরিবেশের প্রশ্নে রাজনৈতিক দলগুলোর জোরালো অবস্থান নেওয়া জরুরি। দলগুলোকে তাদের নিয়মিত কর্মসূচিতে নদী ও পরিবেশ সুরক্ষার দাবিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আপোষহীন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।
এই সময়ে আমাদের সামনে আরও একটি জাতীয় নির্বাচন উপস্থিত। যে ইশতেহার তৈরি হবে, তাতেও সর্বাগ্রে নদী ও পরিবেশকে গুরুত্ব দিতে হবে। গত সময়ে দু-একটি রাজনৈতিক দল ছাড়া সব দলের ইশতেহারেই খুব ক্ষীণভাবে উপস্থিত হয়েছে নদী ও পরিবেশের প্রসঙ্গ। কারো কারো ইশতেহারে প্রসঙ্গটি ছিল অনুপস্থিত।
নদী ও পরিবেশের সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট ৭টি প্রস্তাব:
১. সংগঠনের সর্বস্তরের সদস্যদের নদী ও পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করা এবং এ সংক্রান্ত আইনগুলো নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা।
২. দলের কোনো সংসদ সদস্য বা জনপ্রতিনিধি নদী দখল, কিংবা পরিবেশের জন্য হুমকিমূলক কোনো কাজে যুক্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৩. সংগঠনের সর্বস্তরের কমিটিকে স্থানীয় নদ-নদী, জলাধার দখল-দূষণ মুক্ত করা ও পরিবেশ সুরক্ষার প্রসঙ্গকে সামনে এনে জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।
৪. বিশেষত দেশের নদ-নদী, হাওর, জলাধার, পাহাড়, বনাঞ্চল সুরক্ষায় ও জলবায়ুর অভিঘাত থেকে বাঁচতে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা দলের গঠনতন্ত্র ও আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে প্রণীত ইশতেহারে গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করতে হবে।
৫. নদী ও পরিবেশ বিষয়ক সরকারি প্রতিষ্ঠান—যেমন: পরিবেশ, বন, মৎস্য, নৌ পরিবহন, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নজরদারি করতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে নেওয়া নানা ধরনের সরকারি প্রকল্পের কার্যক্রমে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে।
৬. আন্তঃসীমান্ত নদীর সঠিক তালিকা প্রণয়ন করে প্রতিবেশী দেশগুলোর কাছ থেকে পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে যৌথ নদী কমিশনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে সরকারকে পরামর্শ দেওয়া। বিশেষত তিস্তা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি করা এবং আগামী বছর গঙ্গা নদী পানি বণ্টন চুক্তি নবায়নকে সামনে রেখে দেশের স্বার্থে সরকারকে আরও দায়িত্বশীল ও কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়াতে চাপ প্রয়োগ করতে হবে।
৭. 'নিজ হাতে মাছ ধরে যারা, জলার মালিক হবে তারা' এই নীতিতে জলমহাল ইজারা প্রথা বাতিল করার পক্ষে এবং চায়না দোয়ারি জালসহ অবৈধ সব ধরণের বিদেশি জাল নিষিদ্ধ করতে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। একইসঙ্গে নদী-পরিবেশ সুরক্ষার এই লড়াইয়ে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন, ব্যক্তিদের পরামর্শ নেওয়া ও তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে উদ্যোগী হতে হবে।




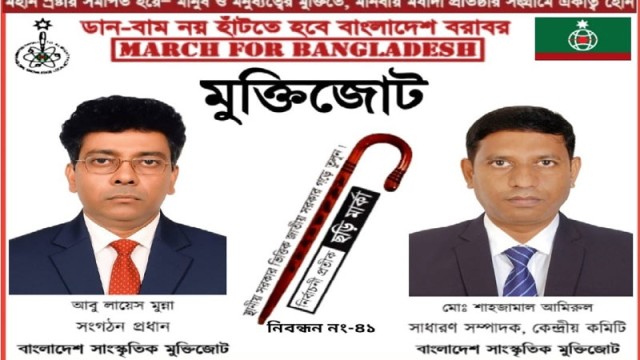

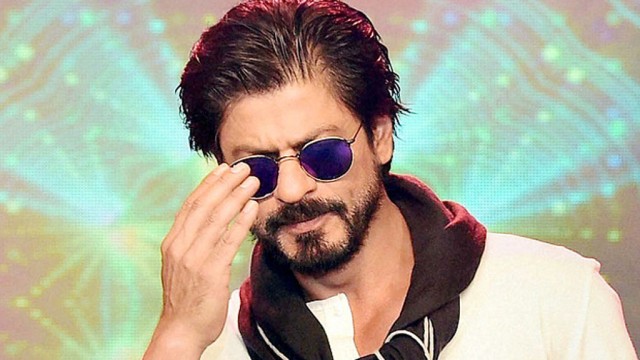










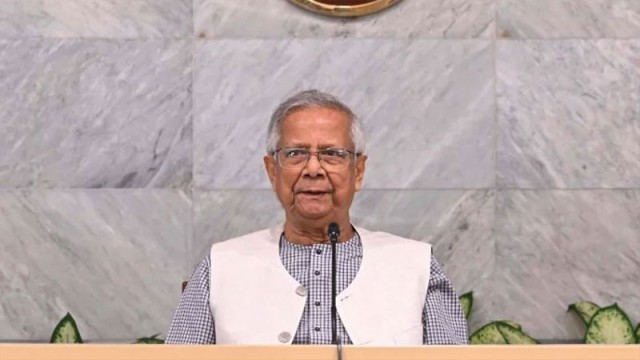











আপনার মূল্যবান মতামত দিন: